Class-7 History Digital Classroom
সপ্তম শ্রেনির ইতিহাস ।। অতীত ও ঐতিহ্য ।।
এই উত্তরপত্র তৈরি করেছেন মেমারি ভি এম ইন্সটিটিউশন, ইউনিট- ওয়ান বিদ্যালয়ের ইতিহাসের শিক্ষক মাননীয় মানস কুমার রায়। যেকোন প্রশ্নের উত্তরের জন্য স্যারের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। whatsapp No- 9734601344
মডেল
অ্যাক্টিভিটি টাস্ক
পরিবেশ ও ইতিহাস (NOV. -2021)
সপ্তম শ্রেণি
পূর্ণমান - ৫০
১. ‘ক’ স্তম্ভের সাথে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও : ১ x ৪ = ৪
১.১ খলিফার অনুমোদন (ক) গিয়াসউদ্দিন বলবন
১.২ সিজদা ও পাইবস (খ) কৃয়দেব রায়
১.৩ বাজারদর নিয়ন্ত্রণ (গ) ইলতুৎমিশ
১.৪ আমুক্তমাল্যদ (ঘ) আলাউদ্দিন খলজি
উত্তর- ১.১- গ) ইলতুৎমিস
১.২- ক) গিয়াসউদ্দিন বলবন
১.৩- ঘ) আলাউদ্দিন খলজি
১.৪- খ) কৃয়দেব রায়
২. বেমানান শব্দটির নিচে দাগ দাও । ১ x ৪ = ৪
২.১ বিজয়ালয়, দন্তিদুর্গ, প্রথম রাজরাজ, প্রথম রাজেন্দ্র। উত্তর- দন্তিদুর্গ
২.২ বরেন্দ্র, হরিকেল, কনৌজ, গৌড়। উত্তর- কনৌজ
২.৩ হলায়ুধ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর। উত্তর- হলায়ুধ
২.৪ প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ইশা খান। বৈরাম খান উত্তর- বৈরাম খান
৩। শূন্যস্থান পূরণ করো : ১ x ৪ = ৪
৩.১ বন্দেগান-ই-চিহলগানির সদস্য ছিলেন সুলতান- গিয়াস উদ্দিন বলবন
৩.২ বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান ছিলেন শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
৩.৩ পোর্তুগিজ পর্যটক পেজ বিজয়নগর পরিভ্রমন করেন।
৩.৪ বিজয়নগর পরাজিত হয়েছিল -তালিকোটার-যুদ্ধে।
৪. সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো : ১ x ৪ = ৪
৪.১ ‘দাগ’ ও ‘হুলিয়া’ ব্যবস্থা চালু রাখেন শেরশাহ। সত্য
৪,২ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে হলদিঘাটির যুদ্ধে আকবর রানা প্রতাপকে পরাজিত করেছিলেন। সত্য
৪.৩ মনসবদারি ও জায়গিরদারি ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল। মিথ্যা
৪.৪ রাজিয়া তার মুদ্রায় নিজেকে ‘সুলতান’ বলে দাবি করেছেন। সত্য
৫. দুই-তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : ২ x ২ = ৪
৫.১ ‘দীন-ই ইলাহি' কী?
উত্তর- ‘দীন-ই ইলাহি’হল মোগল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত একটি ধর্মমত। আকবর সমস্ত ধর্মের সারবস্তু সহযোগে দিন-ই- ইলাহি নামে এই নতুন ধর্ম মতের প্রবর্তন করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বহু ধর্মের পরিবর্তে ভারতে একটি ধর্ম প্রবর্তন করা এবং ধর্মীয় হানা হানি বন্ধ করা। ইবাদত খানার আলোচনা থেকে আকবরের মনে হয়েছিল সমস্ত ধর্মের সারকথা এক। আকবরের এই নতুন ধর্মমতে ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী কিছু নিয়মাবলী বা বিধান ছিল। তাই অনেকে বলেন যে আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। তবে একথা ঠিক নয়।
৫.২ ‘মনসব' কী?
উত্তর- আকবরের শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদ গুলিকে বলা হত মনসব। আর পদাধিকারীদের বলা হত মনসবদার। মনসবদারদের কর্তব্য ছিল বাদশাহের জন্য সৈন্য প্রস্তুত রাখা, সৈন্যদের দেখাশোনা করা এবং যুদ্ধের সময় সৈন জোগান দেওয়া। পদ অনুসারে মনসবদার দের বিভিন্ন স্তর ছিল। সব চেয়ে উপরের পদগুলি শুধুমাত্র রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য রাখা হত। উচ্চ পদস্থ মনসবদারদের বলা হত আমির।
৬. চার-পাঁচটি বাক্যে উত্তর দাও : ৩ X ৫ = ১৫
৬.১ পাল-সেন যুগে কেমন ভাবে কর আদায় করা হত ?
উত্তর- পাল যুগে রাজারা উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তাঁরা নিজেদের ভগের জন্য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসেবে আদায় করতেন। বনিকরাও তাদের ব্যবসা বানিজ্যের জন্য রাজাকে কর দিত। এই তিন প্রকার কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর আদায় করা হত। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের উপর ও কর দিতে হত গ্রাম বাসীদের। এছাড়া হাট এবং খেয়াঘাটের উপরে কর চাপানো হত।
৬.২ সেন রাজারা কি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?
উত্তর- সেন যুগে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর গীতগােবিন্দম্ কাব্যের বিষয় ছিলাে রাধা-কৃয়ের প্রেমের কাহিনি। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার আর এক কবি ধােয়ী লিখেছিলেন পবনদূত কাব্য। এ যুগের আরাে তিনজন কবি ছিলেন গােবর্ধন, উমাপতিধর এবং শরণ। এই পাঁচজন কবি একসঙ্গে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞরত্ন ছিলেন। ত্রয়ােদশ শতকের গােড়ায় কবি শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত সদুক্তিকণামৃত গ্রন্থে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতা স্থান পেয়েছে।
৬.৩ ইকতা ব্যবস্থা কী?
উত্তর- ইক্তা ব্যবস্থা হল সুলতানি আমলে প্রচলিত একপ্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা।সুলতান ইলতুতমিসের আমলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সাধারন ভাবে সুলতানি আমলে প্রদেশ গুলিকে বলা হত ইকতা। ইকতার দায়িত্বে থাকতেন যিনি তাকে বলা হত ইকতাদার বা মুকতি বা ওয়ালি। ইকতাগুলিকে ছোট ও বড় এই দুই ভাগে ভাগ করা হত। ছোট ইকতার শাসক শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন। আর বড় ইকতার শাসকদের সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্ব ও পালন করতে হত।
৬.৪ খলজি বিপ্লব বলতে কী বোঝো?
উত্তর- ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি বল্বনের বংশধরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতান হন। এই ঘটনাকে 'খলজি বিপ্লব' বলা হয়। এর ফলে দিল্লিতে ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা চলে যায়। তার বদলে খলজি তুর্কি ও হিন্দুস্তানিদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল।
৬.৫ ‘দাক্ষিণাত্য ক্ষত’ বলতে কী বোঝো?
উত্তর- খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ঔরংজেবের সময়ে মারাঠাদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ঔরংজেব ভেবেছিলেন যে দক্ষিণই রাজ্য গুলিকে জয় করতে পারলে সেখান থেকে অনেক বেশী রাজস্ব আদায় করা যাবে। তার সঙ্গে মারাঠা দের দমন করাও সহজ হবে। ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘলরা বিজাপুর ও গোল্কুন্ডা দখল করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন এত বড়ো আগে কখনও হয়নি। কিন্তু বাদশাহ যা ভেবেছিলেন তা হলনা। তাঁর বদলে বহু বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুঘলদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হল। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের এই ক্ষত আর সারল না। মারাঠা নেতা শিবাজিকেও স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিতে হল। ২৫ বছর ধরে যুদ্ধ করে ঔরঙ্গজেব শেষে দাক্ষিণাত্যেই মারা গেলেন। এই ঘটনাকেই দাক্ষিণাত্য ক্ষত বলা হয়।
৭. আট-দশটি বাক্যে উত্তর দাও : ৫ x ৩ = ১৫
৭.১ বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণের পর বাংলাতে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল?
উত্তর- আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ বা ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি বাংলার নদিয়া দখল করেছিলেন। সেই থেকে বাংলার তুর্কি শাসন শুরু হয়েছিল। তুর্কিরা বিনা যুদ্ধেই নদিয়া জয় করে। এরপর বখতিয়ার নদিয়া ছেড়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহরকে সমকালীন ঐতিহাসিকরা লখনৌতি বলে উল্লেখ করেছেন।
বখতিয়ার খলজি নিজের নতুন রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এইসব শাসনকর্তারা ছিলেন তাঁর সেনাপতি। বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং সুফি সাধকদের আস্তানা তৈরি করে দেন।
লখনৌতি রাজ্যের সীমানা উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে বখতিয়ার খলজি অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর বখতিয়ার খলজি তিব্বত আক্রমণ করে রাজ্যবিস্তার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।
১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি মারা যান। বাংলায় তুর্কি অভিযানের একটা
অধ্যায় শেষ হয়। ঐ একই সময়ে পূর্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনেরও মৃত্যু ঘটেছিল।
৭.২ কৃয়দেব রায়কে কেন বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়?
উত্তর- বিজয়নগর রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম শাসক ছিলেন তুলভ বংশের রাজা কৃষ্ণদেব রায়। তিনি ছিলেন একাধারে সুযযাদ্ধা, বিচক্ষণ কটনীতিবিদ, প্রজাদরদী শাসক ও সংস্কৃতি মনস্কা। তার রাজত্বকালে (১৫০৯-১৫৬০ খ্রীঃ) বিজয়নগর রাজ্য গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। কৃয়দেব রায়কে বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয় তার কারণ গুলি হল-
প্রথমত, কৃষ্ণদেব রায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ।। ইতিপূর্বে কৃষ্ণদেব রায়চুড় দুর্গ দখল করলেও (১৫১২ খ্রীঃ) বিজাপুরের সুলতান ইসমাইল আদিল শাহ রায়চড় দুর্গটি উদ্ধার করেছিলেন। ১৫২০ খ্রীঃ সালুভতিম্মার নেতৃত্বে বিজয়নগর বাহিনী পুনরায় রায়চূড় পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ শুরু করে এবং পর্তুগীজ গোলন্দাজদের সাহায্যে দুর্গটি দখল করে।
দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজ বণিকদের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রেও রাজা কৃষ্ণদেব বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এ সময় পর্তুগীজরা ঘোড়ার ব্যবসায়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল। পর্তুগীজ বণিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে কৃষ্ণদেব রায় উন্নতমানের ঘোড়া লাভ করেন।
তৃতীয়ত, প্রজাদরদী শাসক হিসাবেও কৃষ্ণদেব রায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ লিখেছেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এবং তার যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণতা ছিল। বছরে অন্তত একবার তিনি সারা রাজ্য পরিভ্রমণ করে প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনতেন। তার এই গণসংযোগ রাজতন্ত্রকে দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছিল।
চতুর্থত, কৃষ্ণদেবের রাজত্বকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দক্ষিণ ভারতে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। তিনি স্বয়ং ছিলেন তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত। একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে তিনি সংস্কৃত, কানাড়ী, মালায়ালমসহ দক্ষিণ ভারতের সমস্ত ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করতেন। তেলেগু সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদেব রায়ের আমলে যে অগ্রগতি সূচিত হয় তার জন্য একে ‘তেলেগু ভাষার স্বর্ণযুগ’ বলে চিহ্নিত করা হয়। কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং ‘আমুক্তমাল্যদা’ ও ‘জামবতী কল্যাণম্’ নামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন।
পঞ্চমত, স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য ও চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদেব রায়ের আমলেও ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। হাজারস্বামী মন্দির’, কৃষ্ণ মন্দির, বিলস্বামী মন্দির’ প্রভৃতি তার স্থাপত্য কীর্তি ও ধর্মভাবনার নিদর্শন বহন করে। বিঠঠলস্বামী মন্দিরটির কারুকার্য ছিল বিস্ময়কর। তাছাড়া বিজয়নগর শহরে বহু সুরম্য প্রাসাদ তার আমলে নির্মিত হয়।
প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদেব রায়ের ব্যক্তিগত কর্মকুশলতার জন্যই বিজয়নগর সাম্রাজ্য গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছায়।
৭.৩ শেরশাহের যে-কোনো দুটি প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর- শের শাহের (১৫৪০-৪৫ খ্রিঃ) সংস্কার শেরশাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার অনেকটা মিল ছিল। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় শের শাহ কিছু সংস্কার করেছিলেন।
শের শাহ কৃষককে ‘পাট্টা’ দিতেন। এই পাট্টা-য় কৃষকের নাম, জমিতে কৃষকের অধিকার, কত। রাজস্ব দিতে হবে প্রভৃতি লেখা থাকত। তার বদলে কৃষক রাজস্ব দেওয়ার কথা কবুল করে। কবুলিয়ত নামে অন্য একটি দলিল রাষ্ট্রকে দিত।
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে শের শাহ সড়কপথের উন্নতি করেন। তিনি বাংলার সোনারগাঁ থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সড়ক সংস্কার করান। রাস্তাটির নাম ছিল ‘সড়ক-ই আজম। এই রাস্তাই পরবর্তীকালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত হয়। এছাড়াও আগ্রা থেকে যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত একটি সড়ক তৈরি হয়। লাহােরথেকে মুলতান পর্যন্ত আরও একটি রাস্তা তৈরি হয়। পথিক ও বণিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে ধারে অনেক সরাইখানা তৈরি করা হয়েছিল।
শের শাহ ঘোড়ার মাধ্যমে ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন।
সেনা বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে ‘দাগ’ ও ‘হুলিয়া’ ব্যবস্থা না, চালু রাখেন শের শাহ।
সপ্তম
শ্রেণি ইতিহাস (OCT-2021)
১. ‘ক’ স্তম্ভের সাথে
‘খ’ স্তম্ভ মেলাও : ১x৪=৪
ক- স্তম্ভ ‘খ’ স্তম্ভ
১.১ পানিপতের প্রথম যুদ্ধ
(ক) ১৫২৯ খ্রি:
১.২ খানুয়ার যুদ্ধ। (খ) ১৫২৬ খ্রি:
১.৩ ঘর্ঘরার যুদ্ধ। (গ) ১৫৩৯ খ্রি:
১.৪ চৌসার যুদ্ধ (ঘ) ১৫২৭ খ্রি:
উত্তর- ১.১- খ)
১৫২৬
১.২- ঘ)১৫২৭
১.৩- ক)১৫২৯
১.৪- গ)১৫৩৯
২. শূন্যস্থান পূরণ
করো : ১x৪=৪
২.১ আদিল শাহের প্রধানমন্ত্রী
হিমু দিল্লি দখল করেছিলেন।
২.২ আকবর পানিপতের দ্বিতীয় যুদ্ধে আফগানদের হারিয়ে দেন।
২.৩ মুঘলরা কান্দাহারের উপর
নিয়ন্ত্রণ হারায় শাহজাহানের আমলে।
২.৪ মুঘলরা বিজাপুর ও গোলকোন্ডা
দখল করে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে।
৩. দু-তিনটি বাক্যে
উত্তর দাও : ২ X ৩=৬
৩.১ ‘জাবতি’ কী?
উত্তর- মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে নতুন করে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণের নিয়ম চালু হয়। একে বলা হয় 'জাবতি' প্রথা। 'জাবত' মানে নির্ধারণ।
৩.২ ‘মনসব’কী ?
উত্তর- আকবরের শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসনিক পদ গুলিকে বলা হত মনসব। আর পদাধিকারীদের বলা হত মনসবদার। মনসবদারদের কর্তব্য ছিল বাদশাহের জন্য সৈন্য প্রস্তুত রাখা, সৈন্যদের দেখাশোনা করা এবং যুদ্ধের সময় সৈন জোগান দেওয়া। পদ অনুসারে মনসবদার দের বিভিন্ন স্তর ছিল। সব চেয়ে উপরের পদগুলি শুধুমাত্র রাজপরিবারের সদস্যদের জন্য রাখা হত। উচ্চ পদস্থ মনসবদারদের বলা হত আমির।
৩.৩ বারো-ভূঁইয়া নামে কারা
পরিচিত ছিলেন?
উত্তর- মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে বাংলার স্থানীয় হিন্দু জমিদার ও আফগান্রা মুঘলদের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করেছে।এই বিদ্রোহীরা একসঙ্গে বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, কেদার রায়, ইশা খান প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য।
৪. চার-পাঁচটি বাক্যে
উত্তর দাও : ৩ x ২=৬
৪.১ আবুল ফজল ও আবদুল কাদির
বদাউনি কারা ছিলেন?
উত্তর- আকবরের আমলের দুই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন আবুল ফজল এবং আব্দুল কাদির বদাউনি।আবুল ফজল আল্লামি (১৫৫১-১৬০২ খ্রিঃ) তাঁর লেখা আকবরনামায় তিনি আকবরের প্রশংসাই করেছেন।কিন্তু যে কোনো সময়ের ইতিহাস জানতে হলেশুধুভালো কথা জানলেই হয় না। সেযুগের সমস্যার কথাও জানতে হয়। এই ধরনের সমালোচনা পাওয়া যায় সে যুগের আর একজন ঐতিহাসিক আবদুল কাদির বদাউনির(১৫৪০-১৬১৫ খ্রিঃ) মুন্তাখাবউৎ তওয়ারিখ বইতে। এঁরা দুজনেইমুঘল দরবারে এসেছিলেন ১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু আবুল ফজল হয়ে উঠেছিলেন আকবরের প্রিয় পাত্র। এই ঘটনার দু-ধরনের বিবরণ পাওয়া যায় এঁদের দুজনের লেখায়।
৪.২ তুমি কী মনে করো যে রাজপুত নীতির দ্বারা মুঘলরা ভারতীয় শাসকদের মুঘল প্রশাসনের অঙ্গীভূত করেছিল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।
উত্তর- মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন বুঝেছিলেন যে, হিন্দুস্তানের ক্ষমতা দখল গেলে রাজপুত রাজাদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখা দরকার।কারণ রাজপুতরাই ছিল উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চলের জমিদার।
আকবরের রাজপুত নীতি
পরে এই ধারণা থেকেই বাদশাহ আকবর মৈত্রী ও যুদ্ধনীতির সাহায্যে রাজপুতদের মনসবদারি ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এলেন। মুঘল বাদশাহ ও শাহজাদাদের সঙ্গে কোন কোনো রাজপুত পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হলো। এক্ষেত্রে আকবর নতুন কিছু করেননি। এর আগেও মুসলমান শাসকদের সঙ্গে হিন্দু রাজপরিবারের মেয়েদের বিয়ে হতো। আকবর নিজের স্ত্রীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার বজায় রেখেছিলেন। তিনি হিন্দুদের ওপর থেকে তীর্থ কর ও জিজিয়া কর তুলে নেন। যুদ্ধবন্দিদের জোর করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করাও তিনি নিষিদ্ধ করেন। এতে সাম্রাজ্যের অ-মুসলমান প্রজারা খুশি হয়েছিল। তবে মেওয়াড়ের রানা প্রতাপ সিংহ আকবরের অধীনতা স্বীকার করেননি।
আকবরের নীতির ফলে মুঘলরা বীর রাজপুত যোদ্ধাদের পাশে পেয়েছিল। রাজপুতরাও ওয়াতনের বাইরে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র সুনামের সঙ্গে কাজ করার ও বীরত্ব দেখানোর সুযোগ পায়। মুঘল বাদশাহের সার্বভৌম ক্ষমতা স্বীকার করে নিলে রাজপুতরা ওয়াতনের ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারত। তবে কোনো রাজপুত রাজ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে গোলমাল হলে মুঘলরা সেই রাজ্য সাময়িকভাবে পুরোপুরি হাতে নিয়ে নিত। তারপর মুঘল বাদশাহের ইচ্ছা অনুযায়ী গদিতে নতুন শাসক বসতেন।
খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে জাহাঙ্গির ও শাহজাহান আকবরের রাজপুত নীতিকেই অনুসরন করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে মেওয়াড়ে মুঘলদের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রানা প্রতাপের ছেলে অম্র সিংহ উঁচু মনসব পেয়েছিলেন। শাহজাহানের আমলে রাজপুত সর্দাররা দূর মধ্য এশিয়াতেও লড়াই করতে গিয়েছিল। এই আমলেও রাজপুতদের উঁচু পদ দেওয়া হত।
ঔরঙ্গজেবের আমলে রাজপুত নীতি
ঔরঙ্গজেবের সময়ে সবচেয়ে
বেশি সংখ্যায় রাজপুতরা মুঘল মনসবদারি ব্যবস্থার আওতায় এসেছিল। অম্বরের মির্জা রাজা
জয়সিংহ ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত অভিজাতদের মধ্যে একজন। মারওয়াড়ের রাঠোর। রাজপুত
রানা যশোবন্ত সিংহ প্রথমে বাদশাহের বিরোধী ছিলেন। তবে পরে তিনি মোটা রকমের মনসব পেয়েছিলেন।
তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকার নিয়ে মারওয়াড়ের রাজধানী যোধপুরে গন্ডগোল শুরু হয়।
মুঘলরা ওই রাজ্যটি পুরোপুরি হাতে নিয়ে নেয়। এর ফলে শুরু হয় রাঠোর যুদ্ধ (১৬৭৯ খ্রিঃ)।
এই যুদ্ধে গোড়ার দিকে মেওয়াড় রাজ্য মারওয়াড়ের পক্ষে ছিল। রাঠোর যুদ্ধ মুঘলদের
পক্ষে লাভজনক হয়নি। উপরন্তু, আকবর জিজিয়া কর তুলে নেওয়ার একশো বছর পরে ঔরঙ্গজেব
আবার জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন (১৬৭৯ খ্রিঃ)। অর্থাৎ, আকবর থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘলদের
রাজপুত নীতিতে অনেক মিল ছিল। আবার, কোনো কোনো দিকে অমিলও ছিল।।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
মডেল
অ্যাক্টিভিটি টাস্ক- September-2021
সপ্তম
শ্রেণি ইতিহাস।
১.
বেমানান শব্দ বা নামটি চিহ্নিত করো : ১ X ৩ = ৩
১.১ বাবর, হুমায়ুন,
শেরশাহ, আকবর উত্তর-
১.২ প্রতাপাদিত্য, কেদার
রায়, ইশা খান, বৈরম
খান। উত্তর-
১.৩ জাবত, কানুনগো,
কারোরী, জিজিয়া উত্তর-
২। সত্য
বা মিথ্যা নির্ণয় করো : ১ X ৩ = ৩
২.১ ‘দাগ’ ও
‘হুলিয়া’ ব্যবস্থা
চালু রাখেন শেরশাহ। সত্য
২.২ ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে
হলদিঘাটির যুদ্ধে আকবর রানা প্রতাপকে
পরাজিত করেছিলেন। সত্য
২.৩ মনসবদারি ও
জায়গিরদারি ব্যবস্থা বংশানুক্রমিক ছিল।
মিথ্যা
৩।সংক্ষেপে
উত্তর দাও (৩০-৫০টি শব্দ) : ২X২ =৪
৩.১ ‘দাক্ষিণাত্য ক্ষত’ বলতে
কী বোঝো?
উত্তর- খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতকে ঔরংজেবের সময়ে মারাঠাদের শক্তি অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ঔরংজেব ভেবেছিলেন যে দক্ষিণই রাজ্য গুলিকে জয় করতে পারলে সেখান থেকে অনেক বেশী রাজস্ব আদায় করা যাবে। তার সঙ্গে মারাঠা দের দমন করাও সহজ হবে। ঔরঙ্গজেবের আমলে মুঘলরা বিজাপুর ও গোল্কুন্ডা দখল করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন এত বড়ো আগে কখনও হয়নি। কিন্তু বাদশাহ যা ভেবেছিলেন তা হলনা। তাঁর বদলে বহু বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে মুঘলদের অনেক আর্থিক ক্ষতি হল। দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের এই ক্ষত আর সারল না। মারাঠা নেতা শিবাজিকেও স্বাধীন রাজা বলে মেনে নিতে হল। ২৫ বছর ধরে যুদ্ধ করে ঔরঙ্গজেব শেষে দাক্ষিণাত্যেই মারা গেলেন। এই ঘটনাকেই দাক্ষিণাত্য ক্ষত বলা হয়।
৩.২ ‘দীন-ই
ইলাহি’
কী?
উত্তর-‘দীন-ই ইলাহি’ হল মোগল সম্রাট আকবর প্রবর্তিত একটি ধর্মমত। আকবর সমস্ত ধর্মের সারবস্তু সহযোগে দিন-ই- ইলাহি নামে এই নতুন ধর্ম মতের প্রবর্তন করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বহু ধর্মের পরিবর্তে ভারতে একটি ধর্ম প্রবর্তন করা এবং ধর্মীয় হানা হানি বন্ধ করা। ইবাদত খানার আলোচনা থেকে আকবরের মনে হয়েছিল সমস্ত ধর্মের সারকথা এক। আকবরের এই নতুন ধর্মমতে ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী কিছু নিয়মাবলী বা বিধান ছিল। তাই অনেকে বলেন যে আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন। তবে একথা ঠিক নয়।
৪.
নিজের ভাষায় লেখো (১০০-১২০টি শব্দ) :
শেরশাহের
যে-কোনো দুটি প্রশাসনিক
সংস্কার সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর- শের শাহের (১৫৪০-৪৫ খ্রিঃ) সংস্কার শেরশাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজস্ব ব্যবস্থা ও জনহিতকর কাজের সঙ্গে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সম্রাট আকবরের শাসনব্যবস্থার অনেকটা মিল ছিল। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব ব্যবস্থায় শের শাহ কিছু সংস্কার করেছিলেন।
শের শাহ কৃষককে ‘পাট্টা’
দিতেন। এই পাট্টা-য় কৃষকের নাম, জমিতে কৃষকের অধিকার, কত। রাজস্ব দিতে হবে প্রভৃতি
লেখা থাকত। তার বদলে কৃষক রাজস্ব দেওয়ার কথা কবুল করে। কবুলিয়ত নামে অন্য
একটি দলিল রাষ্ট্রকে দিত।
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে শের শাহ সড়কপথের
উন্নতি করেন। তিনি বাংলার সোনারগাঁ থেকে উত্তর-পশ্চিম
সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সড়ক সংস্কার করান। রাস্তাটির নাম ছিল ‘সড়ক-ই
আজম। এই রাস্তাই পরবর্তীকালে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে খ্যাত হয়। এছাড়াও আগ্রা
থেকে যোধপুর এবং চিতোর পর্যন্ত একটি সড়ক তৈরি হয়। লাহােরথেকে মুলতান পর্যন্ত আরও
একটি রাস্তা তৈরি হয়। পথিক ও বণিকদের সুবিধার
জন্য রাস্তার ধারে ধারে অনেক সরাইখানা তৈরি করা হয়েছিল।
শের শাহ ঘোড়ার মাধ্যমে
ডাক-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছিলেন।
সেনা বাহিনীর উপর নিয়ন্ত্রণ
রাখতে ‘দাগ’ ও ‘হুলিয়া’ ব্যবস্থা না, চালু রাখেন শের শাহ।
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক- 2021
ইতিহাস সপ্তম শ্রেণি
১.
‘ক’ স্তম্ভের সাথে ‘খ’ স্তম্ভ মেলাও :
ক- স্তম্ভ খ-স্তম্ভ
১.১ খলিফার অনুমোদন (ক) গিয়াসউদ্দিন বলবন
১.২ সিজদা ও
পাইবস (খ)
কৃয়দেব রায়
১.৩ বাজারদর
নিয়ন্ত্রণ (গ) ইলতুৎমিশ
১.৪ আমুক্তমাল্যদ (ঘ) আলাউদ্দিন খলজি
২। শূন্যস্থান
পূরণ করো :
২.১ বন্দেগান-ই-চিহলগানির সদস্য ছিলেন সুলতান ------
২.২ বাংলার প্রথম
স্বাধীন সুলতান ছিলেন--শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ
২.৩ পোর্তুগিজ
পর্যটক----পেজ-----বিজয়নগর পরিভ্রমন করেন।
২.৪ বিজয়নগর পরাজিত
হয়েছিল---তালিকোটার-যুদ্ধে।
৩.
সংক্ষেপে উত্তর দাও (৩০-৫০ টি শব্দ):
৩.১ ইকতা ব্যবস্থা
কী ?
উত্তর- ইক্তা ব্যবস্থা হল সুলতানি আমলে প্রচলিত একপ্রকার প্রশাসনিক ব্যবস্থা।সুলতান ইলতুতমিসের আমলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। সাধারন ভাবে সুলতানি আমলে প্রদেশ গুলিকে বলা হত ইকতা। ইকতার দায়িত্বে থাকতেন যিনি তাকে বলা হত ইকতাদার বা মুকতি বা ওয়ালি। ইকতাগুলিকে ছোট ও বড় এই দুই ভাগে ভাগ করা হত। ছোট ইকতার শাসক শুধু সামরিক দায়িত্ব পালন করতেন। আর বড় ইকতার শাসকদের সামরিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি প্রশাসনিক দায়িত্ব ও পালন করতে হত।
৩.২ খলজি বিপ্লব
বলতে কী বোঝ?
উত্তর- ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে জালাল উদ্দিন ফিরোজ খলজি বল্বনের বংশধরদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়ে সুলতান হন। এই ঘটনাকে 'খলজি বিপ্লব' বলা হয়। এর ফলে দিল্লিতে ইলবারি তুর্কি অভিজাতদের ক্ষমতা চলে যায়। তার বদলে খলজি তুর্কি ও হিন্দুস্তানিদের ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছিল।
৪.
নিজের ভাষায় লেখা (১০০ - ১২০ টি শব্দ) :
কৃষ্ণদেব রায়কে কেন বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ
শাসক বলা হয়?
উত্তর- বিজয়নগর রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম শাসক ছিলেন তুলভ বংশের রাজা কৃষ্ণদেব রায়। তিনি ছিলেন একাধারে সুযযাদ্ধা, বিচক্ষণ কটনীতিবিদ, প্রজাদরদী শাসক ও সংস্কৃতি মনস্কা। তার রাজত্বকালে (১৫০৯-১৫৬০ খ্রীঃ) বিজয়নগর রাজ্য গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করে। কৃয়দেব রায়কে বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয় তার কারণ গুলি হল-
প্রথমত, কৃষ্ণদেব রায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল
বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে জয়লাভ।। ইতিপূর্বে কৃষ্ণদেব রায়চুড় দুর্গ দখল করলেও (১৫১২
খ্রীঃ) বিজাপুরের সুলতান ইসমাইল আদিল শাহ রায়চড় দুর্গটি উদ্ধার করেছিলেন। ১৫২০ খ্রীঃ
সালুভতিম্মার নেতৃত্বে বিজয়নগর বাহিনী পুনরায় রায়চূড় পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ শুরু
করে এবং পর্তুগীজ গোলন্দাজদের সাহায্যে দুর্গটি দখল করে।
দ্বিতীয়ত, পর্তুগীজ বণিকদের
সাথে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রেও রাজা কৃষ্ণদেব বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। এ সময় পর্তুগীজরা
ঘোড়ার ব্যবসায়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব অর্জন করেছিল। পর্তুগীজ বণিকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ
নীতি গ্রহণ করে কৃষ্ণদেব রায় উন্নতমানের ঘোড়া লাভ করেন।
তৃতীয়ত, প্রজাদরদী শাসক হিসাবেও
কৃষ্ণদেব রায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমসাময়িক পর্তুগীজ পর্যটক পায়েজ লিখেছেন,
তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন এবং তার যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণতা ছিল। বছরে অন্তত একবার
তিনি সারা রাজ্য পরিভ্রমণ করে প্রজাদের অভাব অভিযোগ শুনতেন। তার এই গণসংযোগ রাজতন্ত্রকে
দৃঢ় ভিত্তি দিয়েছিল।
চতুর্থত, কৃষ্ণদেবের রাজত্বকালে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে
দক্ষিণ ভারতে এক নবযুগের সূচনা হয়েছিল। তিনি স্বয়ং ছিলেন তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষায়
পণ্ডিত। একজন সাহিত্যসেবী হিসেবে তিনি সংস্কৃত, কানাড়ী, মালায়ালমসহ দক্ষিণ ভারতের
সমস্ত ভাষার চর্চাকে উৎসাহিত করতেন। তেলেগু সাহিত্যের বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষ্ণদেব রায়ের
আমলে যে অগ্রগতি সূচিত হয় তার জন্য একে ‘তেলেগু ভাষার স্বর্ণযুগ’ বলে চিহ্নিত করা
হয়। কৃষ্ণদেব রায় স্বয়ং ‘আমুক্তমাল্যদা’ ও ‘জামবতী কল্যাণম্’ নামক দুখানি গ্রন্থ
রচনা করেন।
পঞ্চমত, স্থাপত্য ভাস্কৰ্য্য ও চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও কৃষ্ণদেব
রায়ের আমলেও ব্যাপক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। হাজারস্বামী মন্দির’, কৃষ্ণ মন্দির,
বিলস্বামী মন্দির’ প্রভৃতি তার স্থাপত্য কীর্তি ও ধর্মভাবনার নিদর্শন বহন করে। বিঠঠলস্বামী
মন্দিরটির কারুকার্য ছিল বিস্ময়কর। তাছাড়া বিজয়নগর শহরে বহু সুরম্য প্রাসাদ তার
আমলে নির্মিত হয়।
প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণদেব রায়ের
ব্যক্তিগত কর্মকুশলতার জন্যই বিজয়নগর সাম্রাজ্য গৌরব ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে পৌঁছায়।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
মডেল অ্যাক্টিভিটি
টাস্ক-2
ইতিহাস সপ্তম
শ্রেণি
নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো:
১. শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন—এই উক্তিটা ঠিক না ভুল? তোমার উত্তরের সপক্ষে দুটি
অথবা তিনটি বাক্য লেখো।
উত্তর- ধর্মীয় দিক থেকে শশাঙ্ক শিবের উপাসক বা শৈব ছিলেন।
বৌদ্ধদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল তা নিয়ে আমরা দু-ধরনের মতের সন্ধান পাই। যেমন—
বৌদ্ধবিদ্বেষী : বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ
‘আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প’, বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’
এবং সুয়ান জাঙ এর ভ্রমণ বিবরণীতে শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তার
বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের হত্যা এবং বৌদ্ধ স্মারক ধ্বংস করার অভিযোগও ওঠে।
বৌদ্ধসহিষ্ণু : শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী
না বলার ক্ষেত্রে। যুক্তিগুলি হল—
(i) সুয়ান জাঙ কর্ণসুবর্ণ নগরে লো-টো-মো-চিহ রক্তমৃত্তিকা
নামক বৌদ্ধ বিহারের সমৃদ্ধি লক্ষ করেছিলেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী হলে এই সমৃদ্ধি ঘটত
না।
(ii) ইৎ সিং শশাঙ্কের
মৃত্যুর মাত্র পঞ্চাশ বছর পর বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উন্নতি লক্ষ করেছিলেন। শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী
হলে এই উন্নতি সম্ভব হত না।।
ওপরের আলােচনা থেকে বােঝা যাচ্ছে যে, শশাঙ্কের সঙ্গে বৌদ্ধদের সুসম্পর্ক না থাকলেও শত্রুতার সম্পর্ক ছিল না।
২. সুলতান মামুদের ১৭ বার ভারত আক্রমণের পিছনে
প্রকৃত কারণ কী ছিল বলে তোমার মনে হয়? (৭০/৮০টি শব্দে লেখ)।
উত্তর- আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ
পর্যন্ত সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারত আক্রমন করেন এই আক্রমণের কারণ ছিল তাঁর নিজের রাজ্যকে
সুন্দর ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা। যদিও সুলতান মাহমুদ ভারতের ইতিহাসে একজন আক্রমণকারী
হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন। কিন্তু তিনি শুধুই একজন যোদ্ধা ছিলেন না। ভারত থেকে তিনি
যেমন প্রচুর সম্পদ লুঠ করেছেন, তেমনি নিজের রাজ্যে ভালো কাজে তা ব্যয় করেছেন। তাঁর
আমলে রাজধানী গজনি এবং অন্যান্য শহরকে সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। মাহমুদ সেখানে প্রাসাদ,
মসজিদ,গ্রন্থাগার, বাগিচা, জলাধার, খাল এবং আমু দরিয়ার (নদী) উপর বাঁধ নির্মাণ করেন।
| তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেন যেখানে শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রদের বৃত্তি দেওয়ার
ব্যবস্থা ছিল।
৩. নীচের শব্দগুলির জন্য দুটি করে বাক্য লেখো
ক) মাৎস্যন্যায় :
উত্তর- মাৎস্যন্যায় : 637 খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের
মৃত্যুর পর বাংলায় শক্তিশালী রাজশক্তির অভাবে একশো বছর ধরে যে অরাজকতা চলেছিল তাকে
মাৎস্যন্যায় বলে।।
এইরূপ নামকরণের
কারণ : জলাশয়ে বড়ো মাছেরা যেমন ছোটো মাছদের খেয়ে বেঁচে থাকে, ঠিক একই রকমভাবে
এই সময় বাংলায় শক্তিশালী ব্যক্তিরা দুর্বলের প্রতি অত্যাচার চালায়। মাছেদের আচরণের
সঙ্গে এই ঘটনার মিল থাকায় একে মাৎস্যন্যায় বলা হয়েছে।
অবসান : 750 খ্রিস্টাব্দে গােপাল বাংলার
রাজা নির্বাচিত হওয়ার সময় থেকে মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটেছিল।
খ) ব্ৰত্মদেয় :
উত্তর দক্ষিণ ভারতের রাজাদের অনেকে স্থানীয় সামন্ত ও ব্রাত্মণদের
সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিতেন। অনেক সময় রাজা ব্রাত্মণদের জমি দান করতেন। ব্রাত্মণরা
অনাবাদী জমি ও জঙ্গল পরিষ্কার করে নতুন জনবসতি তৈরি করতেন। রাজা ব্রাত্মণদের যে জমি
দিতেন তার জন্য ব্রাত্মণদের কর দিতে হত না। রাজার জমিদানের এই ব্যবস্থাকে ব্ৰত্মদেয়
ব্যবস্থা’ বলা হয়।
গ) খিলাফত :
উত্তর খলিফা: হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর তার প্রধান
চার সঙ্গী একে একে মুসলমানদের নেতা নির্বাচিত হন। এঁদের বলা হয় খলিফা।। আরবি ভাষায়
‘খলিফা’ শব্দের অর্থ প্রতিনিধি বা উত্তরাধিকারী।
খিলাফৎ :ইসলাম
ধর্মের ক্ষমতা যেসব অঞলে ছড়িয়ে পড়ে তাকে
বলে দার-উল ইসলাম। খলিফা হলেন দার-উল ইসলামের প্রধান নেতা। খলিফার এই অধিকারের এলাকাকে
বলা হয় খিলাফৎ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
👆 Download Pdf- Click here
মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক-3
ইতিহাস সপ্তম শ্রেণি
১। ক স্তম্ভের
সাথে খ স্তম্ভ মিলিয়ে লেখঃ
উত্তর-
হর্ষচরিত -------- বানভট্ট
গৌড়বাহ---------
বাকপতিরাজ
কিতাব উল হিন্দ-------
অলবিরুনি
২.
বেমানান শব্দটির নিচে দাগ দাও ঃ
(ক)
বিজয়ালয়, দন্তিদুর্গ, প্রথম রাজরাজ, প্রথম রাজেন্দ্র
উত্তর- দন্তিদুর্গ
(খ)
বরেন্দ্র, হরিকেল, কনৌজ, গৌড়
উত্তর-কনৌজ
(গ)
হলায়ুধ, জয়দেব, গোবর্ধন, উমাপতিধর
উত্তর- হলায়ুধ
৩। সংক্ষেপে
(৩০ - ৫০টি শব্দের মধ্যে) উত্তর দাও :
(ক)
পাল-সেন যুগে কেমন ভাবে কর আদায় করা হত?
উত্তর- পাল
যুগে রাজারা উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ কৃষকদের কাছ থেকে কর নিতেন। তাঁরা নিজেদের ভগের
জন্য ফুল, ফল, কাঠও প্রজাদের কাছ থেকে কর হিসেবে আদায় করতেন। বনিকরাও তাদের ব্যবসা
বানিজ্যের জন্য রাজাকে কর দিত। এই তিন প্রকার কর ছাড়াও নানা রকমের অতিরিক্ত কর আদায়
করা হত। নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রজারা রাজাকে কর দিত। সমগ্র গ্রামের
উপর ও কর দিতে হত গ্রাম বাসীদের। এছাড়া হাট এবং খেয়াঘাটের উপরে কর চাপানো হত।
(খ)
সেন রাজারা কি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ?
উত্তর- সেন
যুগে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার কবি জয়দেব সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। তাঁর গীতগােবিন্দম্
কাব্যের বিষয় ছিলাে রাধা-কৃয়ের প্রেমের কাহিনি। লক্ষ্মণসেনের রাজসভার আর এক কবি ধােয়ী
লিখেছিলেন পবনদূত কাব্য। এ যুগের আরাে তিনজন কবি ছিলেন গােবর্ধন, উমাপতিধর এবং শরণ।
এই পাঁচজন কবি একসঙ্গে লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞরত্ন ছিলেন। ত্রয়ােদশ শতকের গােড়ায়
কবি শ্রীধর দাস কর্তৃক সংকলিত সদুক্তিকণামৃত গ্রন্থে বিভিন্ন কবিদের লেখা কবিতা স্থান
পেয়েছে।
৪.
নিজের ভাষায় লেখো (১০০-১২০ টি শব্দের মধ্যে) :
প্রশ্ন-
বখতিয়ার খলজির
বাংলা আক্রমণের পর বাংলাতে কি কি পরিবর্তন ঘটেছিল?
উত্তর- আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ বা
১২০৫ খ্রিস্টাব্দের প্রথম দিকে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি
বাংলার নদিয়া দখল করেছিলেন। সেই থেকে বাংলার তুর্কি শাসন শুরু হয়েছিল। তুর্কিরা বিনা
যুদ্ধেই নদিয়া জয় করে। এরপর বখতিয়ার নদিয়া ছেড়ে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে নিজের
রাজধানী স্থাপন করেন। এই শহরকে সমকালীন ঐতিহাসিকরা লখনৌতি বলে উল্লেখ করেছেন।
বখতিয়ার খলজি
নিজের নতুন রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগের জন্য একজন করে শাসনকর্তা নিযুক্ত
করেন। এইসব শাসনকর্তারা ছিলেন তাঁর সেনাপতি। বখতিয়ার খলজি লখনৌতিতে মসজিদ, মাদ্রাসা
এবং সুফি সাধকদের আস্তানা তৈরি করে দেন।
লখনৌতি রাজ্যের সীমানা উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট
থেকে রংপুর শহর, দক্ষিণে পদ্মা নদী, পূর্বে তিস্তা ও করতােয়া নদী এবং পশ্চিমে বখতিয়ার
খলজি অধিকৃত বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এরপর বখতিয়ার খলজি তিব্বত আক্রমণ করে রাজ্যবিস্তার
করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি।
১২০৬ খ্রিস্টাব্দে
বখতিয়ার খলজি মারা যান। বাংলায় তুর্কি অভিযানের | একটা অধ্যায় শেষ হয়। ঐ একই সময়ে
পূর্ববঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনেরও মৃত্যু ঘটেছিল।
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
এই অধ্যায় এর ক্লাসে ভিডিও দেখতে ক্লিক করো 👈
by banglar siksha web portal Govt. of westbengal Education Department
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস আক্টিভিটি টাস্ক-১
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস আক্টিভিটি টাস্ক-২
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস আক্টিভিটি টাস্ক-৩
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস আক্টিভিটি টাস্ক-৪ Click here👇
https://www.unknownfacts.co.in/p/model-activity-task-4.html
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ক্লাস-(অধ্যায়-৬) class 7 HISTORY chapter 6
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ক্লাস-(অধ্যায়-৭) Class 7 HISTORY chapter 7
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ক্লাস-(অধ্যায়-৭) Class 7 History chapter 7
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ক্লাস-
সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ক্লাস-


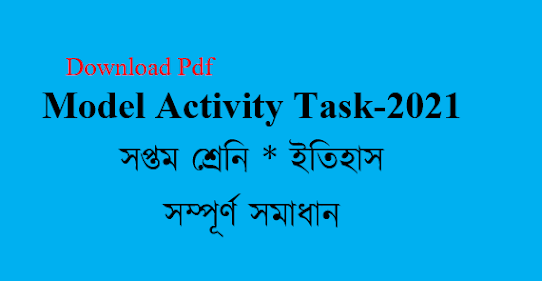






0 Comments